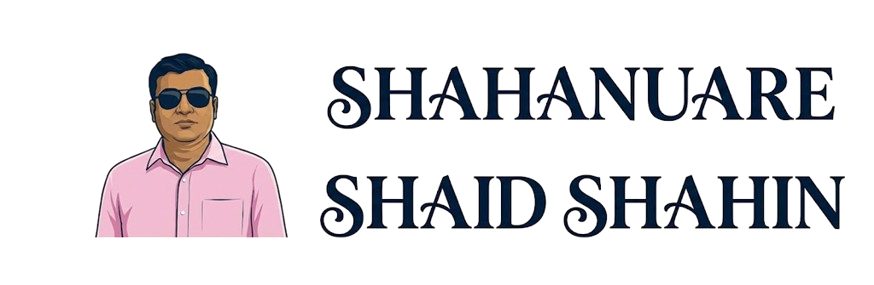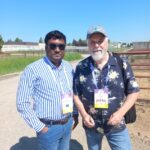সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই ইউক্রেন থেকে গম আমদানির চুক্তি করে বাংলাদেশ সরকার। যুদ্ধের কারণে এই গম পৌঁছানো নিয়ে শঙ্কা থাকলেও দেশটি থেকে গমের প্রথম চালান...
-

-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশে ১৯৭৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রধান দুটি নদীর ভাঙনে বিলীন হয়েছে এক লাখ ৫৭ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমি। এর মধ্যে যমুনায় বিলীন...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের চম্পা রানী মল্লিক ও সরমা রানী। লবণাক্ত পানি ব্যবহারের কারণে চোখ-মুখ জ্বালাপোড়া, পায়ের চামড়া উঠে যাওয়া, চুলকানিসহ নানা ধরনের...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : গত অর্থবছরে গমের আমদানি আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে। তবে আমদানি কমলেও ব্যয় বেড়েছে। এক অর্থবছরের ব্যবধানে গমের আমদানি ব্যয় বেড়েছে প্রায়...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশে মোরগ-মুরগি ও গরু-ছাগলের সংখ্যায় দুই সরকারি সংস্থার হিসাবে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা গেছে। দুই সংস্থার একটি হলো প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস), অন্যটি বাংলাদেশ...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : সাতক্ষীরার আশাশুনির শ্রীউলা ইউনিয়নে গত রবিবার ভ্রাম্যমাণ আদালত চিংড়িতে অপদ্রব্য থাকায় ১৯০ কেজি চিংড়ি মাছ বিনষ্ট করা হয়। এ সময় অপরাধ স্বীকার করায় তিন...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশে মোট উৎপাদিত চালের প্রায় অর্ধেকই আসে আমন মৌসুমে। সেই আমনের বেশির ভাগই আবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে উৎপাদন করা হয়। কিন্তু গত কয়েক দশকের...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : বিশ্বের অন্যতম বড় যুব সংগঠন গ্লোবাল ইয়ুথ পার্লামেন্টের ‘গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’-এর জন্য মনোনীত হয়েছেন কালের কণ্ঠ’র জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন। যুবকদের...
-

চারদিক ধুলায় আচ্ছন্ন। এর মধ্য দিয়েই ভোগান্তি সয়ে কেউ যাতায়াত করছে গাড়িতে, কেউ রিকশায়, কেউবা হেঁটে। গতকাল রাজধানীর তেজগাঁও রেলগেট এলাকা থেকে তোলা। সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : রাজধানীর...
-

(BJAF) President Shahanuare Shaid Shahin : The Bangladesh Agricultural Journalists Forum (BJAF) has announced a 25-day programme to mark its 25th anniversary, including a three-day international agriculture...