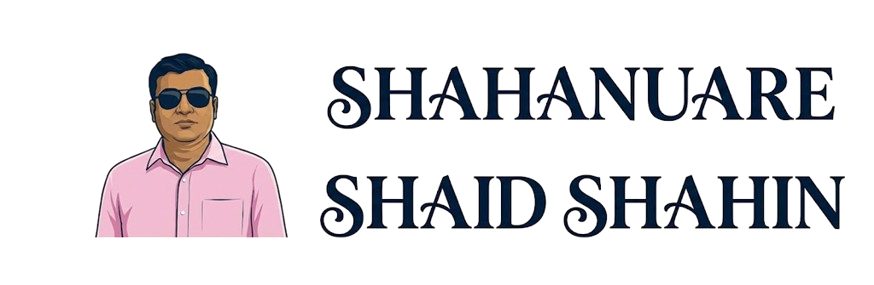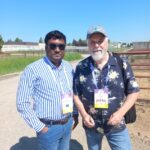বণিক বার্তায় তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদুত মোস্তফা ওসমান তুরান এর সঙ্গে ২২/১১/২০২১ এ বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ ও বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরামের তৎকালীন,সাধারণ সম্পাদক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন এবং...
-

-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে চীন। বাংলাদেশের পঞ্চম শীর্ষ ঋণদাতা এখন চীন। গত অর্থবছরে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ছাড়িয়েছে এক হাজার ৩৬৮ কোটি ডলার।...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশের ৭৬ শতাংশ জমিতে এখন ধানের আবাদ হয়। বাংলাদেশে একজন মানুষ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৬৬ গ্রাম চাল গ্রহণ করছে। সে হিসাবে বছরে একজন মানুষের...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশের মোট নারী শ্রমশক্তির ৭৫ শতাংশ গ্রামে কাজ করে। আর কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতে কাজ করে নারীদের ৭২.৬ শতাংশ। কৃষিতে নারীর এই বিপুল...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : চলতি বছর ধান উৎপাদন কমবে। করোনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে দরিদ্র মানুষ বাড়ছে। ফলে বাড়ছে ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা। এসব...
-

বাংলাদেশ পাবলিক একাডেমির প্রথম সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদান। ২২ নভেম্বর ২০২৪, শুক্রবার, বিকেল ৩টা, স্থান: কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : এ বছরও প্রায় দেড় হাজার ইটখোলায় অবৈধভাবে কাঠ পুড়িয়ে ইট উৎপাদনের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর বাইরে পরিবেশ ছাড়পত্র নেই এমন আরো ইটখোলায় কাঠ পোড়ানোর...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশে গত এক যুগে গরু ও ছাগলের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪২ লাখ। সে তুলনায় মহিষের উৎপাদন পিছিয়ে। এক যুগে মহিষের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখে...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : মেঘনা নদীর তীরে বসবাস জেলে হাবিব হাওলাদারের। গত শুক্রবার মা ইলিশ রক্ষার ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে মধ্যরাতেই ট্রলার নিয়ে মেঘনা গিয়ে ইলিশ ধরতে ফেলেন...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশে কয়েক বছর ধরে সুপারির উৎপাদন ক্রমেই বাড়ছে। এর সঙ্গে বড় হচ্ছে বাজার। ২০২০-২১ অর্থবছরে সুপারির উৎপাদন ছিল তিন লাখ ৫৮ হাজার ৮৪৭ টন।...