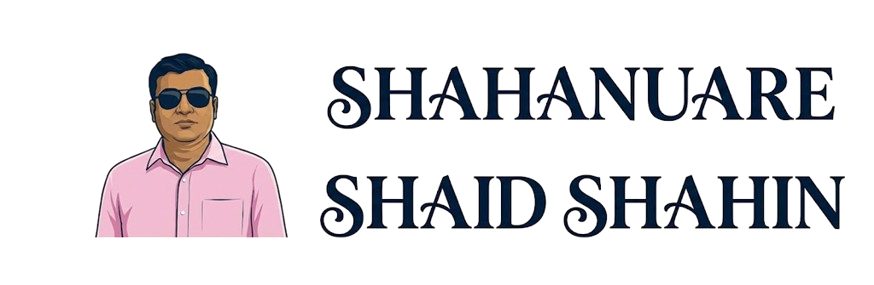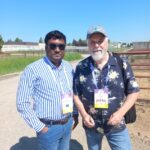সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের সময় দেশগুলোর সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয় বাণিজ্যিক সুবিধা হারানো। এর ধারাবাহিকতায় তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হন রফতানিকারকরা।...
-

-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার। দূষিত হচ্ছে ভূউপরিস্থ পানি। ক্ষতির মাত্রা বিবেচনায় বেশকিছু কীটনাশকের আমদানি ও ব্যবহার এরই মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : সবশেষ আমন মৌসুমে দেশে ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। সরকারের গুদামে বর্তমানে ১৭ লাখ টনের বেশি চাল মজুদ রয়েছে, যা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সরকারের...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : ইউরিয়া সারের দাম কেজিতে ছয় টাকা বাড়ায় চলতি আমন ও পরবর্তী বোরো মৌসুমে চাল উৎপাদনে কৃষকের এক হাজার ৬০০ কোটি টাকা খরচ বাড়বে। কৃষি...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : বিশ্বে চাল উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে ধান আবাদে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সারের ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে প্রতি হেক্টর জমিতে গড়ে প্রায় ৩১৮ কেজি সার ব্যবহার...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : পেয়ারা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে এখন সপ্তম। ২০২০-২১ অর্থবছরে ফলটির উৎপাদন ছাড়িয়েছে ২৪ কোটি ৪০ লাখ কেজি। প্রতি কেজি পেয়ারার ভোক্তা ও পাইকারি বাজারের গড়...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : দেশে খাওয়ার মুরগি উৎপাদন বেড়েছে। গত অর্থবছরে খামারে উৎপাদিত মুরগির সংখ্যা ৩৭ কোটি ৫৬ লাখ ছাড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মুরগি উৎপাদনে এখন তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ।...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী গড় বায়ুদূষণে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ শহরের মধ্যে উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। এই শহরের বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে প্রায়...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : এক দশক আগেও দেশে ড্রাগন ফলের উৎপাদন তেমন ছিল না। বছর ছয়েক আগে বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হওয়া এই ফলের উৎপাদন ছাড়িয়েছে এক কোটি কেজি...
-

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন : খাদ্য উৎপাদন ঘিরে যে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠছে, তাতে খাবারের জোগানের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে শতকোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন...